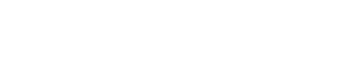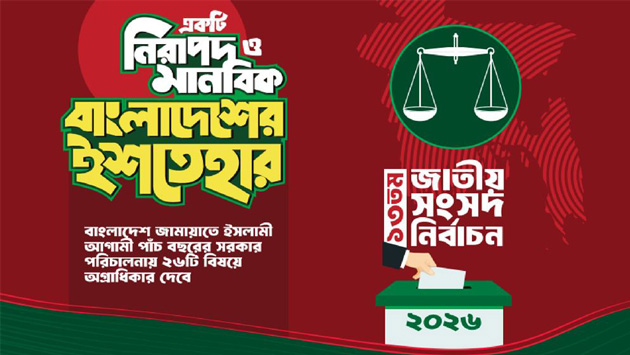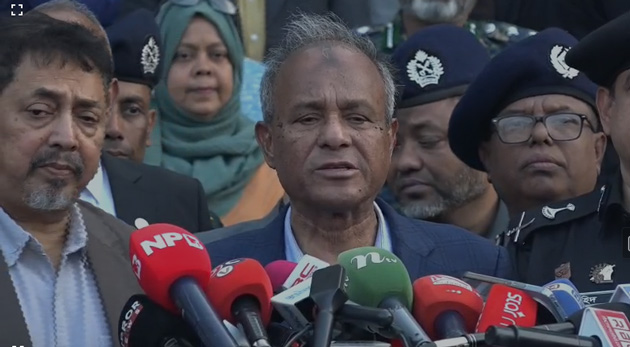পিআর ইস্যুতে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব তীব্র: জামায়াত বনাম বিএনপি

- জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলন: পিআর ছাড়া নির্বাচন নয়।
- বিএনপি: পিআর নয়, প্রচলিত সরাসরি ভোট চলুক।
- ঐকমত্য কমিশন: উচ্চকক্ষে পিআর চালুর প্রস্তাব।
- ইসি: সংবিধানে না থাকায় পিআর সম্ভব নয়।
- বিশেষজ্ঞরা: বাংলাদেশে পিআর অস্থিতিশীলতা ও স্বৈরতন্ত্র ডেকে আনতে পারে।
বদিউল আলম লিংকন: আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে ভোট পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন উচ্চকক্ষে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বভিত্তিক (Proportional Representation–PR) পদ্ধতি চালুর সিদ্ধান্ত দিলেও, এ নিয়ে মতভেদে বিভক্ত হয়ে পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলো।
জামায়াত-ইসলামী আন্দোলনের দাবি
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ দাবি তুলেছে—উভয় কক্ষেই পিআর পদ্ধতি চালু করতে হবে। পিআর ছাড়া নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না। এ দাবিতে তারা আলোচনার পাশাপাশি রাজপথেও কর্মসূচি পালন করছে। গত ১৯ জুলাই ঢাকার মহাসমাবেশে জামায়াত সাত দফা দাবির মধ্যে পিআরের কথা উল্লেখ করে। ইসলামী আন্দোলনের মহাসচিব ইউনুস আহমাদও ঘোষণা দেন, “নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতেই হতে হবে।”
বিএনপির বিরোধিতা
অন্যদিকে বিএনপি পিআর ব্যবস্থার কড়া বিরোধিতা করছে। ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে দলটি আনুষ্ঠানিকভাবে ‘নোট অব ডিসেন্ট’ দিয়েছে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, নিম্নকক্ষে প্রচলিত সরাসরি ভোটই চলবে, আর উচ্চকক্ষে পিআরের সিদ্ধান্তে তাদের আপত্তি থাকবে। ক্ষমতায় গেলে বিএনপি নিজেদের মতো করে ব্যবস্থা নির্ধারণ করবে।
কমিশন ও বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য
ঐকমত্য কমিশনের সদস্য ও সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বলেন, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের প্রস্তাব অনুযায়ী নিম্নকক্ষ থাকবে সরাসরি ভোটে এবং উচ্চকক্ষ হবে পিআরে। তবে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, কোনো ব্যবস্থাই একেবারে নিখুঁত নয়। সম্প্রতি গণমাধ্যমে প্রকাশিত বক্তব্যে তাঁকে উদ্ধৃত করে বলা হয়, পিআর পদ্ধতি “ভয়ঙ্কর” এবং এতে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দীন শনিবার বলেন, সংবিধানে পিআরের কোনো উল্লেখ নেই। তাই আইন পরিবর্তন ছাড়া এ পদ্ধতিতে নির্বাচন সম্ভব নয়।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কাজী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমানের মতে, পশ্চিমা দেশগুলোতে পিআর চালুর মূল উদ্দেশ্য আঞ্চলিক দলগুলোর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হলেও বাংলাদেশের মতো দেশে এই ব্যবস্থা উপযোগী নয়।
তাঁর মতে, পিআর হলে জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচনের পরিবর্তে দলীয় প্রধানদের হাতে মনোনয়নের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবে, যা নতুন করে স্বৈরতন্ত্রের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই বিতর্ক মূলত রাজনৈতিক কৌশল, জনগণের স্বার্থ নয়। কারণ-
জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলনের মতো ছোট দলগুলো জানে সরাসরি ভোটে (FPTP) তাদের আসন পাওয়ার সুযোগ খুব সীমিত। তাই তারা পিআর ব্যবস্থার মাধ্যমে ন্যূনতম ভোট পেলেও সংসদে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে চায়।
বিএনপি বা বড় দলগুলো পিআরের বিপক্ষে, কারণ এতে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের সম্ভাবনা কমে যাবে। ফলে ক্ষমতার ভাগাভাগিতে বাধ্য হতে হবে।
বিশেষজ্ঞরা যেটা বলছেন, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ—পিআর হলে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষমতা আরও কেন্দ্রীভূত হয়ে যাবে দলের শীর্ষ নেতাদের হাতে। এতে গণতন্ত্র নয়, বরং স্বৈরাচারী প্রবণতা বাড়ার ঝুঁকি থাকবে।
বাংলাদেশে সরাসরি ভোটই সবচেয়ে বাস্তবসম্মত পদ্ধতি। তবে উচ্চকক্ষে যদি কোনো সংস্কারের প্রয়োজনে পিআর চালু করা হয়, তবে তা সীমিত আকারে এবং স্পষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে হওয়া উচিত। নাহলে এটি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বাড়াবে, ছোট দলের স্বার্থ রক্ষা করবে বটে, কিন্তু জনগণের ম্যান্ডেটকে দুর্বল করবে।