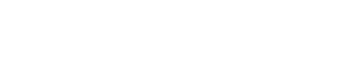কৃষিতে কীটনাশকের ব্যবহার উদ্বেগজনক: রাসায়নিকের অন্ধ আধিপত্য

বিষাক্ত ফল-শস্যে ছড়াচ্ছে মৃত্যুর ছায়া।
বদিউল আলম লিংকন: বাংলাদেশের কৃষি খাতে রাসায়নিক কীটনাশকের অতিরিক্ত ও অসংযত ব্যবহার একটি গুরুতর জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশগত সংকটের সৃষ্টি করছে। ফল-শস্য উৎপাদনে এই রাসায়নিকের ব্যাপক প্রয়োগ শুধুমাত্র উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করছে না, বরং খাদ্যশৃঙ্খলায় বিষাক্ততা ছড়িয়ে দিয়েছে, যা ক্যান্সার, স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী রোগের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।
সাম্প্রতিক গবেষণা ও প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, দেশের সবজি ও ফলের ২৯ শতাংশের বেশি নমুনায় কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ পাওয়া গেছে, যার মধ্যে ৭৩ শতাংশেরও বেশি সর্বোচ্চ সীমা (MRL) অতিক্রম করেছে।
ব্যবহারের বিস্তার: এক দশকের যাত্রা
বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় স্থানে সবজি উৎপাদনে এবং দশম স্থানে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফলের উৎপাদনে উন্নীত হলেও, এই অর্জনের পিছনে রয়েছে রাসায়নিকের অন্ধ আধিপত্য। ১৯৯০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে কীটনাশকের ব্যবহার পাঁচগুণ বেড়েছে, যার মধ্যে অর্গানোফসফরাস, পাইরেথ্রয়েড এবং কারবামেট গ্রুপের রাসায়নিকগুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে।
ক্লরপাইরিফস, ডাইমেথোয়েট, ডায়াজিনন এবং ম্যালাথিয়নের মতো বিষাক্ত পদার্থগুলো সবজি চাষে সাধারণত ব্যবহার হয়, বিশেষ করে টমেটো, বেগুন, লাউ, ফুলকপি, শসা, আলু, গাজর, পেয়াজ, লঙ্কা, পালং শাক, লাউয়ের ফুল এবং সবুজ শাকের মতো ফসলে।
একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, সবজির ১৫৭৭ নমুনার মধ্যে ৪৫৮টিতে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ ছিল, যার মধ্যে লাউয়ে ১০০ শতাংশ, শিমে ৯২ শতাংশ, টমেটোয়ে ৭৮ শতাংশ এবং বেগুনে ৭৩ শতাংশ নমুনা MRL অতিক্রম করেছে।
কৃষকরা প্রায়ই প্রস্তাবিত প্রত্যাহারকাল (withdrawal period) না মেনে কাজ করেন, যার ফলে ফসলে রাসায়নিকের ঘনত্ব বেড়ে যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পোকামাকড়ের আক্রমণ বেড়েছে, যা কৃষকদের আরও বেশি রাসায়নিকের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফলে, সবজি চাষে কীটনাশকের ব্যবহার অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি।
ফলের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি ভালো নয়। ক্যালসিয়াম কার্বাইড, অক্সিটোসিন এবং ইথোফেনের মতো রাসায়নিক অপরিপক্ব ফল পাকানোর জন্য ব্যবহার হচ্ছে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। একটি জরিপে দেখা গেছে, রাজশাহী ও যশোরের টমেটো চাষকারীরা ২৫০০-৮০০০ ppm ইথোফেন ক্যালসিয়াম কার্বাইড ১-৩ দিন আগে ব্যবহার করেন, যা ফলের পুষ্টিমান কমিয়ে দেয় এবং বিষাক্ততা ছড়ায়।
স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ঝুঁকি: একটি নীরব হুমকি
রাসায়নিকের অতিরিক্ত ব্যবহার শুধু কৃষকদের জন্যই নয়, সাধারণ মানুষের জন্যও বিপজ্জনক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী ১০ লক্ষ মানুষ কীটনাশকের কারণে বিষাক্ত হন, যার মধ্যে অর্ধেক কৃষক এবং বাকি খাদ্য ও পানির মাধ্যমে। বাংলাদেশে এই রাসায়নিক খাদ্যের মাধ্যমে মুখে প্রবেশ করে স্নায়ুতন্ত্র, রক্তব্যাধি, এন্ডোক্রাইন ডিসরাপশন এবং প্রজনন সমস্যা সৃষ্টি করে। গাজীপুরের কৃষি জমিতে সংগৃহীত সবজির নমুনায় ভারী ধাতু, কীটনাশক এবং অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী প্যাথোজেন পাওয়া গেছে, যা খাদ্যচক্রে প্রবেশ করে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়াচ্ছে।
পরিবেশের ক্ষতি আরও গভীর। রাসায়নিক মাটি ও পানিকে দূষিত করে, প্রাকৃতিক শিকারী (যেমন মৌমাছি, পাখি) ধ্বংস করে এবং ফসলের ফলন হ্রাস করে। বাংলাদেশে বার্ষিক ৩৭.২৫৮ বিলিয়ন টন কীটনাশক এবং ২.৩২ বিলিয়ন কেজি রাসায়নিক সার ব্যবহার হয়, যা মাটির উর্বরতা কমিয়ে দিচ্ছে। ফলে, কৃষকরা আরও বেশি রাসায়নিকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন।
সরকারি উদ্যোগ ও চ্যালেঞ্জ
সরকার জৈব কীটনাশক এবং সমন্বিত বালাইব্যবস্থাপনা (IPM) প্রচার করছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE) এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) জৈব চাষের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, যাতে রাসায়নিকের ব্যবহার কমানো যায়। উদাহরণস্বরূপ, গাজীপুরের শ্রীপুরে কৃষকরা কেঁচো সার (ভার্মি কম্পোস্ট) ব্যবহার করে সফলতা অর্জন করছেন। তবে, চ্যালেঞ্জ বড়। কৃষকদের মধ্যে সচেতনতার অভাব, রাসায়নিকের সস্তা দাম এবং বাজারের চাপ এই উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করছে।
২০০৯ সালে ৪৫,১৭২ মেট্রিক টন কীটনাশকের ব্যবহার ২০২০ সালে ৩৭,৪২২ মেট্রিক টনে নেমেছে, কিন্তু এখনও অতিরিক্ত।
পথের উপায়: জৈব চাষের দিকে অগ্রসর হওয়া
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জৈব কৃষিকে প্রসারিত করতে হলে কৃষকদের প্রশিক্ষণ, জৈব সারের সহজলভ্যতা এবং বাজার সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। IPM পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক শত্রু (যেমন ফেরোমোন) ব্যবহার করে রাসায়নিকের নির্ভরতা কমানো যায়। সরকারের পক্ষ থেকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বলছেন, “আমরা জৈব কীটনাশকের উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ নিচ্ছি, কিন্তু কৃষকদের সচেতনতা ছাড়া এটি সম্ভব নয়।”
বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতির মেরুদণ্ড, কিন্তু রাসায়নিকের অন্ধকার ছায়া এর উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে ম্লান করে তুলছে। সময়মতো পদক্ষেপ না নিলে, এই সংকট জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে।
সকলের সমন্বিত চেষ্টায় একটি নিরাপদ, টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার সময় এখন।