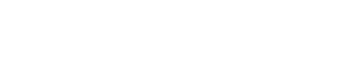পুতিনকে কড়া হুমকি দিলেন ট্রাম্প

টুইট ডেস্ক: ১৪ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইঙ্গিত দেন, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ নিয়ে তাঁর নীতিতে আমূল পরিবর্তন আসছে। তিনি ঘোষণা করেন, ইউক্রেনে যুক্তরাষ্ট্র যে পরিমাণে আকাশ প্রতিরক্ষা ইউনিট পাঠানো হয়েছে, তার বাইরে অতিরিক্ত ইউনিট পাঠানো হবে।
বর্তমানে ইউক্রেনের শহরগুলো প্রতিদিন শতাধিক রুশ ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার শিকার হচ্ছে। হোয়াইট হাউস থেকে ফাঁস হওয়া নথি থেকে জানা যাচ্ছে, ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। ট্রাম্প ফোনালাপে জেলেনস্কির কাছে জানতে চেয়েছেন, মস্কোতে সরাসরি আঘাত হানতে ইউক্রেনের কী ধরনের অস্ত্র প্রয়োজন।
ট্রাম্প একই সঙ্গে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর সবচেয়ে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যদি ক্রেমলিন ৫০ দিনের মধ্যে, অর্থাৎ ৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে যুদ্ধবিরতিতে না আসে, তাহলে যারা রাশিয়ার তেল কিনবে, তাদের ওপর তিনি ১০০ শতাংশ ‘সেকেন্ডারি ট্যারিফ’ বা বাড়তি শুল্ক আরোপ করবেন।
কিন্তু ট্রাম্পের এ কঠিন শাসানি বাস্তবে বিশেষ কোনো কাজে দেবে বলে মনে হচ্ছে না। রুশ কর্মকর্তারা ট্রাম্পের মস্কোতে হামলার হুমকি নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে রীতিমতো হাস্যকর প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। কারণ, ইউক্রেনে যুক্তরাষ্ট্র আকাশ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম পাঠালে তা ইউক্রেনের জন্য কিছুটা সহায়তা হবে বটে, কিন্তু ট্রাম্প যেভাবে বলছেন, সেভাবে বিশাল পরিসরে তা সরবরাহ করতে কয়েক মাস লেগে যাবে।
আর তেল নিষেধাজ্ঞা নিয়ে ট্রাম্প যে হুমকি দিয়েছেন, তা বাজারে কোনো বড় প্রভাব ফেলেনি।
ট্রাম্প যদি সত্যিই যুদ্ধের গতিপথ পাল্টাতে চান, তাহলে তাঁকে ইউক্রেনকে আরও বেশি সমর্থন দিতে হবে। তিনি বলছেন, রাশিয়ার প্রতি তাঁর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। কিন্তু সেটি কি কেবল কথার কথা হিসেবে থাকবে, না কি বাস্তবে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে? আদতে এই প্রশ্নের জবাব ট্রাম্প তাঁর মিত্রদের সঙ্গে কতটা একজোট হয়ে কাজ করতে পারেন এবং পুতিনের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য কতটা মূল্য দিতে রাজি হন, তার ওপর নির্ভর করছে।
রাশিয়ার প্রতি ট্রাম্পের অবস্থানে এ পরিবর্তন আসাটা খুব একটা অপ্রত্যাশিত নয়। ব্যক্তিগতভাবে ট্রাম্প রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতি সহানুভূতিশীল মনে হলেও ইউক্রেন ও রাশিয়া–সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি মূলত যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। আর এটি পুতিনের অবস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীত।
ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি বাড়াতে চান। অন্যদিকে পুতিনও, বিশেষ করে ইউরোপের পাইপলাইন বাজার হারানোর পর তাঁর দেশের গ্যাস রপ্তানি বাড়াতে চাইছেন।
গ্যাস রপ্তানি বাড়ানোর কথা মাথায় রেখে ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ডকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। এ কারণে তিনি ভবিষ্যতের আর্কটিক নৌপথগুলোকে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। অন্যদিকে রাশিয়াও চীনের সমর্থন ধরে রাখতে তাদের নিজস্ব আর্কটিক রুটকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। পুতিন ইউক্রেনের যতটা সম্ভব খনিজ সম্পদ রাশিয়ার জন্য দখল করতে চান। ট্রাম্পও সেই খনিজ সম্পদ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নিশ্চিত করতে চান।
প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ট্রাম্প বলেছিলেন, এক দিনেই তিনি ইউক্রেন-রাশিয়া সংঘাত মেটাবেন। এখন তিনি নিজেই স্বীকার করছেন, সংঘাত মেটানোর সময়টা আরেকটু বাড়িয়ে বলা উচিত ছিল।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির প্রতি ট্রাম্পের মনোভাব অতীতে খুব ভালো ছিল না। এর মূল পেছনের ঘটনা হলো ২০১৯ সালের ‘ইমপিচমেন্ট কেলেঙ্কারি’। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি জেলেনস্কিকে চাপ দিয়েছিলেন যেন ইউক্রেনে বাইডেন ও তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত শুরু করা হয়, কিন্তু জেলেনস্কি তা শোনেননি। এ ঘটনা মার্কিন রাজনীতিতে প্রচণ্ড আলোড়ন তোলে এবং ট্রাম্প প্রথমবার ইমপিচমেন্টের মুখে পড়েন। তখন থেকেই জেলেনস্কিকে ট্রাম্প ‘বিশ্বাসযোগ্য’ মনে করতেন না।
কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলেছে। ইউক্রেনের সরকার, বিশেষ করে জেলেনস্কি, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত চুক্তি করেছে, যার মূল বিষয় হলো ইউক্রেনের খনিজ সম্পদ।
ইউক্রেনের মাটিতে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ খনিজ রয়েছে (যেমন লিথিয়াম, যা ব্যাটারি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়) এবং যুক্তরাষ্ট্র এসব খনিজ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে আগ্রহী। এ সমঝোতা ট্রাম্পের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এতে মার্কিন স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে। ফলে জেলেনস্কির প্রতি তাঁর পুরোনো বিরূপ মনোভাব অনেকটাই নরম হয়ে এসেছে।
কিছুটা দেরিতে হলেও ট্রাম্প এখন বুঝতে পেরেছেন, পুতিন আন্তরিকভাবে কোনো আলোচনা করতে চান না। মে ও জুন মাসে কিয়েভ ও মস্কোর মধ্যে শান্তি আলোচনা হলেও তাতে কোনো অগ্রগতি হয়নি।
ট্রাম্প যখনই দেখেছেন, পুতিন আলোচনার সময় অনেক বেশি দাবি করছেন, সম্ভবত ট্রাম্প তখনই উপলব্ধি করেছেন, রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা আর এগোনো সম্ভব হবে না। ট্রাম্প বুঝতে পেরেছেন, পুতিন শুধু দক্ষিণ ও পূর্ব ইউক্রেনের দখল করা অঞ্চলগুলো ধরে রাখতে চাচ্ছেন না; বরং নতুন করে উত্তর ইউক্রেনে একটি ‘বাফার জোন’ও গড়ে তুলতে চাইছেন।
রাশিয়া প্রশ্নে ট্রাম্পের পরিবর্তিত অবস্থানের তেমন প্রভাব দেখা না যাওয়ার প্রধান দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, রাশিয়ার তেলের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের একার বাড়তি শুল্ক আরোপের হুমকি মানুষের কাছে কোনোভাবে বিশ্বাসযোগ্য হবে না। কারণ, ট্রাম্প নিজেই সব সময় তেলের দাম বাড়া নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন। গত জুনে যখন যুক্তরাষ্ট্র ইরানে সামরিক হামলা চালায়, তখন বিশ্ববাজারে তেলের দাম বেড়ে যায়। এর পরপরই ট্রাম্প প্রকাশ্যে বলেন, তিনি এ মূল্যবৃদ্ধিতে ‘অসন্তুষ্ট’। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি নিজের রাজনৈতিক অবস্থান ঠিক রাখতে তেলের দাম বাড়ানোর মতো পদক্ষেপ নিতে চান না। তাই রাশিয়ার তেল নিয়ে এ কঠিন হুমকিও বাস্তবে কার্যকর হতে পারে, এটি সবাই বিশ্বাস করবে না।
দ্বিতীয়ত, এ হুমকির কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ আছে। ট্রাম্প আগে একই কৌশল ভেনেজুয়েলার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছিলেন। মার্চ মাসের শেষ দিকে তিনি বলেছিলেন, যারা ভেনেজুয়েলার তেল কিনবে, তাদেরও তিনি শাস্তি দেবেন। এতে প্রথমে কিছুটা প্রভাব পড়ে, তেল রপ্তানি কিছু কমে যায়। কিন্তু এরপর চীন ওই তেল বেশি করে কিনতে শুরু করে, ফলে আবার ভেনেজুয়েলার রপ্তানি বেড়ে যায়।
রাশিয়ার ক্ষেত্রেও একই সমস্যা। রাশিয়ার সবচেয়ে বড় তেল ক্রেতা চীন। কিন্তু চীন ও ট্রাম্প ইতিমধ্যে একধরনের ‘শুল্কযুদ্ধ’-এ জড়িয়ে আছেন। অর্থাৎ ট্রাম্প চীনের ওপর নানা ধরনের আমদানি শুল্ক বসাচ্ছেন এবং চীনও পাল্টা ব্যবস্থা নিচ্ছে। এমন অবস্থায় চীন যদি দেখে, ট্রাম্প আবার রাশিয়ার তেল নিয়ে নতুন শুল্ক চাপাতে চাইছেন, তাহলে তারা সেটা পাত্তাই দেবে না; বরং তারা আরও বেশি করে রাশিয়ার তেল কিনে রাশিয়ার পাশে দাঁড়াতে পারে।
আসলে ট্রাম্পকে নিজের কৌশল বদলাতে হবে। রাশিয়ার ওপর এমন অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে হবে, যা পুতিনকে আন্তরিকভাবে আলোচনায় বসতে বাধ্য করবে। তবে সেটি একা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে করা সম্ভব হবে না। এর জন্য ওয়াশিংটনকে তার মিত্রদের নিয়ে কাজ করতে হবে। কিন্তু ওয়াশিংটন এখন তার মিত্র ও অংশীদারদের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে লিপ্ত। ফলে এটি এখন আরও কঠিন হয়ে পড়েছে।
অবস্থাদৃষ্টে বোঝা যাচ্ছে, রাশিয়ার তেলের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা চাপানো সহজ হবে না। কারণ রাশিয়া এমন কিছু মানবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভারতকে প্রভাবিত করার সুযোগ আছে। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর আগে ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে খুব বেশি তেল কিনত না। কিন্তু এখন ভারতের আমদানি করা তেলের প্রায় ৪০ শতাংশই আসে রাশিয়া থেকে। এখন রাশিয়া ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল সরবরাহকারী হয়ে উঠেছে।
ভারতের জ্বালানিমন্ত্রী হারদীপ সিং পুরি গত সপ্তাহে বলেছেন, ভারত আপাতত তাদের তেল নীতিতে কোনো পরিবর্তন আনবে না। তবে তিনি এটাও বলেছেন, এর আগে যখন তেলের দামের ওপর সর্বোচ্চ সীমা বসানো হয়েছিল, তখন ভারত তা মান্য করেছিল। জি-৭ দেশগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে সেই সীমা নির্ধারণ করেছিল বাইডেন প্রশাসন। এর উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ার তেল বিক্রি বন্ধ না করে তাদের আয় সীমিত রাখা। কারণ, জি–৭ দেশগুলো চায়নি তেলের বাজারে অস্থিরতা তৈরি হোক। এখন ট্রাম্পও একই কারণে তেলের বাজারে বড় কোনো ঝাঁকুনি দিতে চান না। এমনকি বাইডেনের অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেনও তখন বলেছিলেন, এর লক্ষ্য ছিল এই ব্যবস্থায় ভারতসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশ যেন সস্তায় তেল কিনতে পারে, তার ব্যবস্থা করা।
তবে মন্ত্রী পুরি এও বলেছেন, যদি রাশিয়ার তেল নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে কোনো বড় সমঝোতা হয়, তাহলে ভারত নিজেদের নীতিতে পরিবর্তন আনতে পারে।
এই পরিস্থিতিতে, যদি ট্রাম্প তাঁর রাশিয়ার বিরুদ্ধে হুমকি সত্যি করে তুলতে চান, তাহলে তাঁকে একা কিছু না করে অন্য মিত্রদের সঙ্গে মিলে যৌথভাবে কাজ করতে হবে।
ট্রাম্প যদি সত্যিই যুদ্ধের গতিপথ পাল্টাতে চান, তাহলে তাঁকে ইউক্রেনকে আরও বেশি সমর্থন দিতে হবে। তিনি বলছেন, রাশিয়ার প্রতি তাঁর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। কিন্তু সেটি কি কেবল কথার কথা হিসেবে থাকবে, না কি বাস্তবে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে? আদতে এই প্রশ্নের জবাব ট্রাম্প তাঁর মিত্রদের সঙ্গে কতটা একজোট হয়ে কাজ করতে পারেন এবং পুতিনের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য কতটা মূল্য দিতে রাজি হন, তার ওপর নির্ভর করছে।